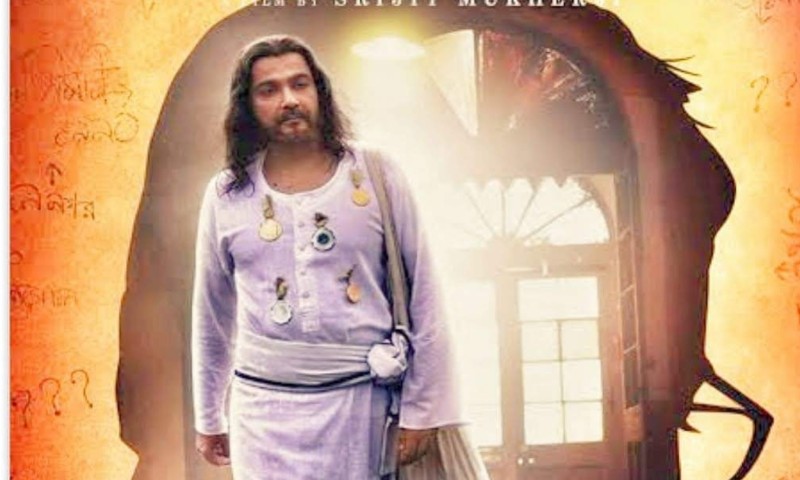রানা চক্রবর্তীঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রধানতঃ তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল, (ক) সশস্ত্র বিপ্লব – চরমপন্থা আন্দোলন, (খ) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস গণ আন্দোলন, এবং (গ) নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখ সমর। এছাড়া আঞ্চলিক স্তরে তখন যেসব আন্দোলন দেখা দিয়েছিল সেগুলো সবই উপরোক্ত ঐ তিনটি প্রধান ধারায় গিয়ে মিলিত হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান তিনটি ধারায় শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ইতিহাস থেকে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যতদিনে নিজের সংঘটিত রূপ নিয়েছিল, ততদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন ক্রগাগতঃ নিজের স্বর্ণবিভায় বিকশিত হচ্ছিল, যা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরিপূর্ণ ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত, এবং স্বামী বিবেকানন্দের অক্লান্ত প্রয়াসে ও তাঁর সতীর্থ ত্যাগী ও গৃহী পার্ষদদের অপরিমেয় সাহচর্যে প্রসারিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক সূচনাকাল থেকেই শ্রীমা সারদাদেবী সেটির নেতৃত্বে ছিলেন। আসলে তিনিই মিশনের ‘সংঘজননী’ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথানুসারে তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের ‘হাইকোর্ট’। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯২০ সাল – এই দীর্ঘ ৩৪টি বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীমা সারদাদেবী নেতৃত্ব না দিলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পল্লবিত বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটা সম্ভব ছিল না। শ্রীমা সেই সময়ের নানা প্রতিকূলতা, সংকট, প্রতিবন্ধকতার আবহ থেকে রামকৃষ্ণ সংঘকে যেমন মুক্ত করেছিলেন, তেমনি নিজের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপন শক্তির প্রচ্ছায়ায় সেটিকে আগলে রেখেছিলেন। তিনি স-শরীরে বেঁচে থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের উপরে যেসব সংকট ঘনীভূত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল – ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় অগ্নি সংযোগ, এবং সেসবের ক্রম প্রসারিত দ্যুতিতে ভীত রাজশক্তির রোষ। তবে সেই বিষযে বিস্তারিত আলোচনা করবার আগে পূর্ব প্রেক্ষাপটটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।
আরো পড়ুন- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন, (দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব)

ইতিহাস বলে যে, দীর্ঘদিন ধরে পরাধীন থাকবার ফলে ভারতবাসীর আত্মশক্তির ক্ষেত্রে আদর্শায়িত জীবনবোধে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। সেই সময়ে শৈথিল্যের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজনের জীবনে হাজারো স্খলন-পতন নেমে এসেছিল। ধর্মাচরণে নানাবিধ অত্যাচার-অবিচারের মাঝে, সামাজিক বিশৃঙ্খলায় সাধারণ মানুষ নতজানু হয়ে পড়েছিলেন। ভারতের পার্থিব সম্পদ লুণ্ঠনের পাশাপাশি ভারতীয় শাশ্বত জীবনধারায় কালনেমির অভিশাপ নেমে এসেছিল। এই সবের ফলে সংগত কারণেই সাধারণ মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, আর শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা তখন আত্নগত সংকটের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছিলেন। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় তাঁর সমকালীন কলকাতায়, লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের’ সূত্রে প্রজা-শোষণের অর্থে বিত্তশালী স্বল্প সংখ্যক মানুষজনের সাহচর্যে যে নবজাগরণ আনবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা বাস্তবিক ক্ষেত্রে আংশিক – অপূৰ্ণ ছিল। সেই আংশিক ও অপূর্ণ নবজাগরণের সূত্র ধরে তখন কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হলেও সেসব আন্দোলন কখনোই পুরোপুরিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি। অন্ততঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের চিত্রটি সেই সাক্ষ্যই বহন করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, যা কিনা ভারতের ইতিহাসে মহাবিদ্রোহ ও ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, সেই বিদ্রোহের পর থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী-শিক্ষিত মানুষেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নিজেদের বন্ধুর পরিবর্তে শত্রু হিসেবে চিনতে শিখেছিলেন। মজার ব্যাপার হল যে, এর আগে কিন্তু তাঁরাই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসনক্ষমতা দখলে উল্লসিত হয়েছিলেন, এবং সেই পরিবর্তনের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাঁবেদারে পরিণত হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের পরে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটেছিল। তাই তখন দেখা গিয়েছিল যে, বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে, ভাবের ঊর্মিমুখর স্রোতে ভেসে বঙ্গদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। ১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা, ন্যাশনাল পেপারের আত্মপ্রকাশ, ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা – সেটারই ফলশ্রুতি ছিল। সেই সময়ের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকেরা ঐ ভাববাদী মানসিকতা নিয়েই অজস্র নাটক, কাব্য-কবিতা এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তারপরে এসেছিল উপন্যাস। ‘রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়’ তাঁর ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যে সোল্লাসে ঘোষণা করেছিলেন – “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে / কে বাঁচিতে চায়।” ‘সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর’ গান লিখেছিলেন – “মিলি সবে ভারত সন্তান”। ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর’ লিখেছিলেন – “চলরে চল সব ভারত সন্তান”। অতুলপ্রসাদ সেন সরাসরি লিখেছিলেন – “ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে”। সেই ভাববাদী মানসিকতা থেকে একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বাস্তবের মাটির সঙ্গে সংযোগ ঘটানো, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সেটাকে সংযুক্ত করে দেওয়া, অন্যদিকে প্রকৃত অর্থে নবজাগরণের পরিপূর্ণ রূপটি মানুষের সামনে প্রথম যিনি মেলে ধরেছিলেন, তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভাববাদের আঙিনা থেকে সরে এসে ক্রমে তিনিই প্রথম পায়ে পায়ে প্রায় সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছিলেন। তৎকালীন ভারতের প্রকৃত ছবিটি, এবং অতীত ও বর্তমানের ব্যবধানের দীর্ঘ রেখাটি তিনি চিনেছিলেন, জেনেছিলেন ও বুঝেছিলেন। তাই তো বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার ধূলিধূসরিত প্রব্রজ্যার দিনগুলি সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজও বিবেকানন্দের পদচিহ্নের পদাবলী হয়ে রয়েছে। সেই সূত্রেই তিনি পাশ্চাত্যে গমন করেছিলেন। এরপরে দীর্ঘ চার বছর ধরে তিনি পাশ্চাত্যে অবস্থান করেছিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হয়ে প্রতীচ্যের প্রমিথিয়ুস বিবেকানন্দ সামগ্রিকভাবে নিদ্রিত ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। সেখানে ভারতের মর্মবাণী পৌঁছে দিয়ে পাশ্চাত্যের আকাশে-বাতাসে তিনি আলোড়ন তুলেছিলেন, সর্বোপরি মানুষের মনে-প্রাণে ১৮৯৭ সালে তাঁর ভারত-প্রত্যাবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগরণের মন্ত্রটি পূর্ণ ও শুদ্ধ হয়েছিল। তাই সেই নবজাগরণের পূর্ণতায় বিবেকানন্দের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে পরবর্তীকালে ‘ঋষি অরবিন্দ’ লিখেছিলেন, “পশ্চিমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে স্বদেশের সনাতন ধ্যান ধারণার বহু উপাদানের পুনর্মূল্যায়ন ও বর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এই উদ্যোগ। পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছিল ভারতবর্ষের চিন্ময় লোকের তীব্র প্রতিক্রিয়া। কখনো প্রতীচ্য সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যান, কখনো বা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর নতুনভাবে গুরুত্ব আরোপ ও নবতর ব্যঞ্জনার সংযোজন শুরু হয়েছিল। শুধুমাত্র ভারতীয় বলে পুরনো সংস্কৃতির সমস্ত কিছুকে সমর্থন ও জাতীয় জীবনে সেগুলির সাঙ্গীকরণই হয়ে উঠেছিল এই পর্যায়ের চিন্তানায়কদের প্রধান কাজ। এর পরে আরম্ভ হয় আত্মীকরণের এক যুগ্ম প্রক্রিয়া। সনাতন ধ্যান-ধারণাগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন – ঐতিহ্যবাদী ও তার সমালোচক – উভয়পন্থী মানুষের তুষ্টিবিধানের একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যাবর্তনের একটা পূর্ণতর রূপ, একটা সমন্বয়ধর্মী পুনর্ব্যাখ্যার নীতিগ্রহণ করে। তা প্রাচীন সংস্কৃতির বাহ্য আঙ্গিক কোন কোন সময়ে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেও জীর্ণতাকে বর্জন করেছিল। নতুন যা কিছু প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে খাপ খায় বা তাকে বৃহত্তর বিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় তাকেও গ্রহণ করেছিল। বিগত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন এবং পুনর্বিন্যাসের ধারা সংরক্ষণের এই উদ্যোগের প্রাণপুরুষ ছিলেন বিবেকানন্দ।” (ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ: ৩১-৩২) বিবেকানন্দ তাঁর নিজের জীবনের প্রথম পর্বে মিল, বেন্থাম ও কোঁতের মধ্যে মানবব্যাধির নির্ণয় ও নিদান, মানবসমাজের সমস্যা এবং সমাধান ব্যাকুলভাবে খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞানালোককে যেমন তিনি নির্বিচারে বরণ করতে চাননি; তেমনি আবার ভারতের জীর্ণ সংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্বতার প্রতি তাঁর বিরাগও গোপন থাকেনি। সেজন্যই তাঁকে তখন দার্শনিক-অনুসৃত মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে দেখা গিয়েছিল। অনেকের মতে আধ্যাত্মিক জগতে বিবেকানন্দের ভূমিকা শিল্পের রাজ্যে মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে তুলনীয়। বিবেকানন্দকে প্রায়ই বলতে শোনা গিয়েছিল যে, একসময় নিদ্রাবেশে তাঁর সামনে দুটি জীবনাদর্শ ভেসে উঠত। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, এবং অপরটি ছিল সর্বরিক্ত সন্ন্যাসী। প্রাচীন ভারতবর্ষের পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবন, এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানপ্রসূত সকল পার্থিব জীবনের টানাপোড়েনে বিবেকানন্দের মনোজগৎ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। বহুদিন এমনি করেই মাইকেল এঞ্জেলোও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়েছিলেন। গ্রীক-ল্যাটিন- ধ্রুপদী রীতির, নিও-প্লেটোনিক আদর্শবাদ, এবং রেনেসাস পর্বে বাস্তববাদের দ্বন্দ্বে তিনিও দোলায়িত হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবেকানন্দকে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতায় জমজমাট, আকাশের মত নিঃসীম, সমুদ্রের মত অতলান্ত, হীরকখণ্ডের মত সুকঠিন, এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জীবন প্রবাহের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাই বিবেকানন্দ তাঁর নবীন দৃষ্টিতে অতীত ও বর্তমানকে মেলাতে পেরেছিলেন। জাতির জাগরণের তাবৎ মন্ত্রগুলিকে তিনি পাঠ করতে পেরেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপরে এক মহৎ ব্রত পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সেই দায়িত্ব ছিল – বিচার, বিবেক ও উক্তির সাহায্যে পরের মধ্যে নারায়ণকে জাগ্রত করা। সেই জাগরণের মধ্যে দিয়েই বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেবেন – এটাই তাঁর কাম্য ছিল। তাঁর সেই কামনা ব্যর্থ হয়নি। তুষারমৌলি হিমালয় থেকে সমুদ্র-চুম্বিত কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পথের ধূলার মধ্যে তিনি তাঁর অধিষ্ট শিবকে অগণিত নিরন্ন ক্লিষ্ট জীবের মাঝে খুঁজে পেয়েছিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে পৌঁছে তিনি প্রাচীন বেদান্তকে নতুন করে উপস্থাপিত করেছিলেন, রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রচার করেছিলেন; জানিয়েছিলেন যে – সকলেই অমৃতের অধিকারী, ধর্ম অসীম, অনন্ত তার ভাব ও পথ, বহুত্ববোধে মায়ার জন্ম – তার থেকে আসে দুঃখ-ভয়-মৃত্যু; আর এক-রমতা বা সমতাই ঈশ্বর, তিনিই অন্তরে-বাইরে বিরাজমান। বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের জীবন যোগ করবার প্রত্যয়ে তাঁর ঈন্সিত অভীপ্সাই প্রসারিত হয়েছিল। তিনি সগর্বে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত করবার জন্য যে বিপুল কর্মশক্তি দরকার, একমাত্র ভালোবাসাই সেটার উৎস হতে পারে। তাঁর মত ছিল যে, অন্তহীন সর্বপ্লাবী সেই ভালোলাগাই সহস্র ধারায় মানবসেবায় রূপান্তরিত হবে, বিশ্বাস কর্মের মাধ্যমে নিজের রূপ নেবে। আর এই দুই মিলে আগামী দিনের মানুষের চরিত্রকে গড়ে তুলবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে – শক্তি, পৌরুষ, ক্ষাত্র-বীর্য, ব্রহ্মতেজ – এই উপাদানগুলি মানুষের অজেয় সম্পদ হবে। তাই বেদান্তের বিশুষ্ক অনুশীলন নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা সেটাকে যুগের উপযোগী করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করবেন, আর তাতেই মানুষের আত্মশক্তি জেগে উঠবে। বিবেকানন্দ কর্মযোগের সোপান ধরে প্রথমে আত্মশুদ্ধি, এবং পরে ধ্যান-ভজনের সোপান ধরে আত্মপোলব্ধি চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে – সন্ন্যাসী সংসারকে – অন্ন, শিক্ষা, আরোগ্য ও ধর্ম – এই চতুর্বিধ জ্ঞান দেবেন। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের সেই চিন্তাধারাকে – ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, বিশেষতঃ চরমপন্থী সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা নিজেদের জীবনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই ১৯০৯ সালের ২৬ জুন তারিখের ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকায় ঋষি অরবিন্দ লিখেছিলেন, “পৃথিবীকে নিজের দুটি হাতে ধরে তাকে রূপান্তরিত করার জন্য যাঁর আবির্ভাব সেই পরমপুরুষই বিবেকানন্দের বিজয়ের পথ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আর তা সমস্ত বিশ্বের কাছে এই সত্যটা পরিস্ফুট করে দেয় যে ভারতবর্ষ পুনর্জাগ্রত হয়েছে।” সেই নবজাগরণ শুধু টিকে থাকবার জন্য ছিল না, সেটা বিশ্ববিজয়ের মত একটা মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য ছিল। সেই সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থীরা বিবেকানন্দের উচ্চারিত অতুলনীয় মন্ত্রে – “উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত” – প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর ‘গভীর’ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মৃত ল্যাঙ্গারেসের মত তাঁরাও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল যে, মিথ্যে মায়ার মত বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলাও সকলের পবিত্র কর্তব্য। বিবেকানন্দের প্রেরণা তাঁদের মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে শিখিয়েছিল, কেননা বিবেকানন্দের ভাষায় – “আমি মৃত্যুঞ্জয়ী, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বহু ঊর্ধ্বে আমি, আমিই সে।” সেই মন্ত্রই ছিল ভারতীয় শাশ্বত জীবনধারার পবিত্র মন্ত্র। জীবনকে জয় করবার, এবং আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষ্যে উত্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে সেই মন্ত্রই ছিল চরম এবং পরম। বিবেকানন্দই প্রথম ‘জগদ্ধিতায়’ একটি বাস্তব পরিকল্পনা রচনায় সফল হয়েছিলেন। তাঁর দরিদ্রনারায়ণ সেবার মহৎ আদর্শকে ঘিরেই তখন সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ, জাতি এবং শ্রেণীর অনায়াস মিলন সম্ভবপর হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়েই তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, জাত-পাতের দ্বন্দ্বের বিমোচন সম্ভব হয়েছিল। বিবেকানন্দ গীতার সেই শাশ্বত মন্ত্র – “উদ্ধারেৎ আত্মনাত্মনম্” – কখনোই বিস্মৃত হননি। পরহিত সাধনা আত্ম উদ্ধারের পথকেই প্রশস্ত করে। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন, অসুস্থকে সেবা, এবং অজ্ঞকে জ্ঞানদানের মধ্যে দিয়েই মানুষের সহজাত স্বার্থপরতার অবসান ঘটে। কর্ম তখন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য হয়ে ওঠে। ‘ডারউইন’ কথিত নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নয়, এমন নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়েই মানুষের বিবর্তন হয়। তবে অনাহারক্লিষ্টের জন্য অন্নের সংস্থান, কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির সেবার চেয়ে শিক্ষাদান যে বড় – সে বিষয়ে বিবেকানন্দের মনে কখনোই কোন সন্দেহ ছিল না। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সর্ববিধ শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলেই তিনি মনে করতেন। শিক্ষাকে তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশের সহায়ক হিসেবে দেখতেন। আর সব শিক্ষার মূলে রয়েছে ধর্ম। কিন্তু সেটা কি প্রথাগত হিন্দুধর্ম? বিবেকানন্দ বলতেন যে, হিন্দুধর্মের মত অন্য কোন ধর্ম মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে পারেনি। আবার দীনহীনের উপরে নির্যাতন নিপীড়নের ব্যাপারেও হিন্দু ধর্মের জুড়ি পাওয়া যায় না। এই অবিশ্বাস্য স্ববিরোধিতার একমাত্র কারণ হল এই ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অন্যায় প্রয়োগ। হিন্দুধর্মের মধ্যে আচার-সর্বস্ব ভণ্ডরাই অতীতে অসহায়ের উপরে অত্যাচার অবিচার এবং ব্যভিচারের অসংখ্য সুযোগ উদ্ভাবন করেছিলেন। সেই বিষয়ে তাঁরা ওল্ড টেস্টামেন্টের ‘ক্যারিসী’ ও ‘ম্যাডিয়ুসী’দেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধকে জাগিয়ে তুলে সেই কলুষ দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা যেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিক্রমণ করে দীন ও দরিদ্রের কুটিরেই সেই ধর্মের বাণী প্রচার করেন। তাঁরা যেন পতিত চণ্ডালের হৃদয়েও এই মহৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন যে, ব্রাহ্মণদের মত তাঁদেরও ধর্মানুশীলনের অধিকার রয়েছে; তাঁদেরও বিচার বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা রয়েছে, কেননা সকলের মধ্যেই সেই পরম ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। বিবেকানন্দ ভালো করেই জানতেন যে, ওই ভাবে জাতীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে পশ্চিমী সভ্যতার সম্মুখীন হতে গেলে বিকৃতি ও অন্ধ অনুকরণ অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাই তো তিনি বলেছিলেন, “এই পরানুবাদ পরানুকরণ পরমুখাপেক্ষা দাসসুলভ দুর্বলতা এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা – এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?” ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষের প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা আসবে বলে বিবেকানন্দ তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছছিলেন। রাজনৈতিক মুক্তি তো মানব-অস্তিত্বের উপরের স্তরটিকে শুধু স্পর্শ করতে পারে, সেটা কখনোই মানুষের সার্বিক মুক্তির পথটিকে প্রশস্ত করতে পারে না। বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার বলে সার্বিক মুক্তি চেয়েছিলেন। পশ্চিমী জগতের দেশগুলিতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর যে আদর্শ মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এদেশের মানুষের সেটাকে অনুকরণ করাকে এক ধরণের উন্মত্ততা বলে তিনি মনে করতেন। কেননা তৎকালীন ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক অবস্থা পত্তনের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, ঐ সব দেশে বহু আগেই সেটার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। সেই বিষয়ে সেখানে বহু আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছিল, এবং শেষপর্যন্ত সেটা অপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। সেখানে একের পর এক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছিল। ইউরোপ তখন নিজেই দিশেহারা ছিল। ওই সময়ে ‘স্বামী শিবানন্দ’কে লেখা বিবেকানন্দের একটি চিঠিতে সেই সত্যটিই প্রকাশিত হয়েছিল – “তোমাদের পার্লামেন্ট, সিনেট, তোমাদের নির্বাচন, ভোটাধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠতা – সব কিছুর সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। কিন্তু বন্ধু, সর্বত্রই এদের ইতিবৃত্ত পরিণাম একই। সবদেশে পরাক্রান্ত মানুষই নিজের ইচ্ছা অনুসারে সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। বাকী সবাই ভেড়ার পালের মত নিষ্ক্রিয় নির্বিকার।” তখন কোথাও কোথাও অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু যদি না তা ধর্মের উপরে, মনুষ্যত্বের উপরে নির্ভর করতে পারে, তাহলে মানবসভ্যতার অস্তিত্বই যে বিপন্ন হয়ে উঠবে, সেবিষয়ে বিবেকানন্দের কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একমাত্র ধর্মই সমস্ত কিছুর মূলে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। মানুষ যদি ধর্মে সুস্থিত থাকে তবে অন্য সব কিছুই যথাযথ থাকবে। পার্লামেন্টের কোন বিধান দিয়ে তো আর কারো মধ্যে ধর্মানুভূতি জাগানো সম্ভব নয়। সেটার জন্য রাজনীতির চেয়ে ধৰ্ম উপলব্ধি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পার্থিব কোন সুখ সম্পদই আত্মার শূন্যতাকে দূর করতে পারে না। আত্মাকে মলিন রেখে সমস্ত পৃথিবী জয় করলেও সেই ক্ষীণায়ু হয়। সেই জন্য আধ্যাত্মিকতার বিকাশের প্রতি উদাসীন সভ্যতার ভিত্তি চোরাবালির মত হয়। কিন্তু অদ্বৈতবাদ কোন মানুষের আত্মশক্তিকে একবার উদ্বোধিত করে দিলে তাঁর পক্ষে সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন সহজ হয়ে যায়। তখন যে অসীম শক্তির জন্ম হয় সেটার আঘাতে শ্রেণী বৈষম্য, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, এমনকি সাম্রাজ্য পর্যন্ত চূর্ণ হয়ে যেতে পারে। যে আধ্যাত্মিকতা ভারতীয়ত্বের পরম অভিজ্ঞান – সেটার বিনিময়ে নয়, সেটাকে কেন্দ্র হিসেবে রেখে প্রতীচ্যের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মানবহিতৈষণা পরিচালিত হওয়াই কাম্য। রাজনীতি মানুষের মধ্যে প্রকৃত মিলন বা ঐক্যবন্ধন রচনা করতে পারে না, সেটা শুধু সাময়িকভাবে কিছু মানুষকে পাশাপাশি করে দেয়। ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে সেটা এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী জড়বাদের জন্ম দেবে বলে বিবেকানন্দ বহু আগেই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিশিষ্ট বিপ্লবী ‘বিপিনচন্দ্র পাল’, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি আধ্যাত্মিক উদ্যোগ বলেই মনে করতেন। প্রত্যেক মানুষের অন্তঃস্থলে তাঁর অস্তিত্ব বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি রয়েছে। আর ঈশ্বর যেহেতু অনন্তরূপে প্রকাশিত, স্বাধীনতা সেটারই এক প্রকাশ। সেকালের চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এভাবেই বেদান্তের বিশেষ বাণীর ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর ঋষি অরবিন্দের বিচারে স্বরাজের প্রকৃত তাৎপর্য ছিল – আধুনিক পরিবেশে প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জাতীয় গৌরবের সত্যযুগের পুনরুজ্জীবন, বিশ্বমানবের গুরু রূপে তার পূর্ব ভূমিকা পুনর্গ্রহন। ‘ভবানী মন্দির’ শিরোনামের রচনাটিতে অরবিন্দ যে ভবানীর ধ্যান করেছিলেন, সেখানে তিনি ভক্তবৃন্দকে এমন একটি মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন যেটা সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য হবে। আর তার জন্যই ভারতের স্বরাজ লাভ অত্যন্ত জরুরী ছিল। একটি বিষয়াসক্ত, স্বার্থপর, অর্থগৃধু জাতির পার্থিব ও রাজনৈতিক সিদ্ধির ক্রীড়নক হিসেবে নয়, বিশ্বের আত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই ভারতের স্বাধীন অস্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক ছিল; আর সেটার সমস্ত উদ্যোগ, সমস্ত সংগ্রামই জগদ্ধিতায় ছিল। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, সেই প্রেরণাই একটি নবীন জাতির জন্ম দেবে, একটি জুগকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে, এবং সমস্ত পৃথিবীকে ভারত ধর্মের মহামন্ত্রে দীক্ষা দেবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সন্তান দল’-এর ভাবনা ও ‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রটি সংশ্লিষ্ট ভাবধারায় অগ্নিময় বিভা ছড়িয়ে দিয়েছিল।
একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপেই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচিতি। আর সেই ধর্ম হল – “আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ”। প্রচলিত ধর্মের বাইরে বেদান্ত ধর্মের প্রসারেই রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গিয়েছে। সার্বিক মানুষের কল্যাণ, আত্মশক্তির জাগরণ এবং মুক্তি – সূচনাকাল থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এই ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ প্রথমেই মিশনের লিখিত নিয়মাবলীর মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সংযোগ থাকবে না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থী দুই বিশিষ্ট বিপ্লবী – অরবিন্দ ঘোষ এবং বিপিনচন্দ্র পালের মানসিকতা, যা এই প্রবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা থেকেই বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সত্যতা বুঝতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত না হলে সার্বিক ভাবে মানুষের সঙ্গে সংযোগ কখনোই গড়ে তোলা সম্ভব নয়; আর সেই সংযোগ থেকেই গণজাগরণ ও তা থেকে গণ আন্দোলন এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। রবীন্দ্রনাথও সেই উপলব্ধির স্তবে পৌঁছেছিলেন। তাঁর ‘কালান্তরের’ প্রবন্ধগুলি সেটারই পরিচয়বাহী। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, বিবেকানন্দও প্রথম অবস্থাতে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য বৈপ্লবিক পথে পা বাড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনুজ ‘ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত’ নিজে সেই তথ্য ‘সিস্টার ক্রিস্টিন’কে জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, স্বামীজী তখন দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে বৈপ্লবিক পথে ভারত থেকে বৈদেশিক শাসনকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি তখন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন, এবং বন্দুক নির্মাতা ‘হিরাম ম্যাক্সিমের’ সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনও করেছিলেন। কিন্তু তারপরে বিবেকানন্দ যখন দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই দেশ এবং দেশের সাধারণ মানুষ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নন, তখন তিনি মানুষ-জাতি গঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। (Patriot Prophet, Bhupendranath Datta, Forward, P: viii-ix) আসলে বিবেকানন্দ সর্বার্থে এবং সর্বাগ্রে গণজাগরণ চেয়েছিলেন, এবং সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষুধাতুর অজ্ঞ জনগণকে আগে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার সুযোগ দিয়ে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। কারণ, জনগণই যদি না সচেতন হন, জনগণই যদি না জেগে ওঠেন, তবে কাদের নিয়ে, কাদের জন্য আন্দোলন করা? তাঁর সেই চিন্তা পরবর্তীকালের বিপ্লবীদেরও সচেতন করেছিল, তাই দেখা যায় যে – বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল – পরাধীন ভারতের এই তিন প্রধান বিপ্লবী দলের অনুগামীরা চরম পথযাত্রী হয়ে, সশস্ত্র সংগ্রামে সামিল হয়ে অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিজেদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এবং পরবর্তী সময়ে নিজেদের বিপ্লবী মত ও পথ পরিত্যাগ করে শেষপর্যন্ত ‘বিরাট’-এর উপাসনায় মেতে উঠে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস জীবনকে অবলম্বন করে নিয়েছিলেন। তখন তাঁরা ভিন্ন পথে জনসেবা-দেশসেবার মধ্যে দিয়ে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের অভিজ্ঞান – যা কিছু আগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেটা যে কতটা বাস্তবমথিত ও সুদূরপ্রসারী ছিল – এই উদাহরণ থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। অব্যবহিত পরবর্তীকালে অববিন্দ, বিপিনচন্দ্রের জীবন ও কর্মধারা সেই সাক্ষ্যই বহন করে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিরে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে নবীন যুবকদের স্বাধীনতা স্পৃহা লক্ষ্য করে তাঁদের জাতি-দেশ গঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করবার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, “আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরিয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসব ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত …।” (বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৯৮-১৯৯) তিনি বলেছিলেন যে, জনসাধারণের সেবা কবে তাঁদেরকে ‘মানুষ’ কবে তুলতে পারলেই দেশমাতৃকার মুক্তি সম্ভব। স্বামীজী মানুষ চেয়েছিলেন – সেই মানুষ, যাঁরা খাঁটি অকপট মানুষ হবেন; যাঁরা প্রতিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হবেন; যাঁরা অবিচলিত শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন। তিনি মনে কটন যে, যদি অমন একশো আত্মবিশ্বাসী, আদর্শনিষ্ঠ যুবক পাওয়া যায়, তাহলে ভারতের মুক্তি ঘটবেই। তাই ভাবীকালের দেশপ্রেমিকদের সামনে তিনি স্বদেশপ্রেমের একটি নতুন আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। সেটা পশ্চিমের আমদানী করা দেশপ্রেম ছিল না, হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা দেশপ্রেমিকরাও ছিলেন না; তিনি বড়মাপের হৃদয়, প্রত্যয় দৃপ্ত দৃঢ়তা এবং অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে দেশপ্রেমিক হওয়ার উপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের সেই অগ্নিগর্ভ বাণী, ত্যাগ ও বিশ্বাসের আদর্শ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট ক্ষীয়মান মুমূর্ষু জাতির প্রাণে প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও অত্যুগ্র আশার সঞ্চার করে ভারতে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। বিবেকানন্দ তাঁর জীবিতাবস্থাতেই লেভিয়াথানের নিদ্রাভঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, “সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। নিদ্রিত শব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত মস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না – আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে … কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। … কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙিতেছে।” (বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃ- ৩৮) জাতি সত্যিই সেদিন জেগেছিল। বিবেকানন্দের প্রেরণায় ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন পথে ধাবিত হতে শুরু করেছিল। লক্ষ লক্ষ যুবক তখন জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। মিশনের কর্মধারা তখন দেশে-দেশান্তরে বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হচ্ছিল। ইতিহাস বলে যে, সেকালের ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে রামকৃষ্ণ মিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছিল। স্বভাবতই সেই সময়কার সহিংস ও অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সকলেই বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা ও ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন, আর বিপরীতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির রোষবহ্নি ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠেছিল।

বিবেকানন্দের জীবনাবসানের (১৯০২) পরেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কারণে, বঙ্গদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। যার ফলে বিপ্লববাদীরা তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এরপরে নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজী ও বালগঙ্গাধর তিলকের আবির্ভাব ঘটেছিল। ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এখন জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তখন যে মানসিকতা, প্রস্তুতি ও জাতীয় চেতনার প্রয়োজন হয়েছিল, বিবেকানন্দই প্রকৃতপক্ষে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সেই মহত্তর জিনিসটি যুগিয়েছিলেন। ওই সময়কার জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। তখন বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের আস্তানা খানা তল্লাস করতে গিয়ে ব্রিটিশ পুলিশ বিবেকানন্দের গ্রন্থ ও তাঁর আগ্নেয় রচনাসমূহ পেয়েছিল। সেই কারণে ‘সিডিসন কমিটি’র রিপোর্ট (১৯১৮), উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ‘জেমস ক্যাম্বেল কার’ সম্পাদিত ‘Political Troubles in India: 1907-17’ এবং বিভিন্ন গোপন রিপোর্টেও তৎকালীন বিপ্লবীদের উপরে বিবেকানন্দের প্রভাবের সূত্রে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তীব্র রাজরোষের প্রকাশ ইতিহাস থেকে লক্ষ্য করা যায়। তারপরে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট জেলা থেকে প্রদেশ হয়ে রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ‘স্বামী ব্রহ্মানন্দ’ অধ্যক্ষ থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের উপরে পুলিশের প্রবল নজরদারীও ছিল বলে সেই সময়কার গোপন সরকারি রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন কলকাতাস্থ ‘ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের’ পুলিশ প্রধান ‘চার্লস টেগার্টের’ রিপোর্ট, ১৯১৫ সালের ‘বেঙ্গল এডমিনিসট্রেশন রিপোর্ট’ (যেটার ভিত্তিতে ‘লর্ড কারমাইকেল’ তাঁর দরবারী ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন), বাংলা সরকারের লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী ‘সি. টিনড্যাল’, বাংলার চীফ সেক্রেটারী ‘এইচ. এল. স্টিফেনসন’, এবং কাউন্সিলের সদস্য ‘পি. সি. লায়ন’-এর ১৯১৭ সালের রিপোর্টটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন বঙ্গদেশের যুবকেরা বিবেকানন্দের বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সহিংস ও অহিংস – দুই আন্দোলনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিবেকানন্দকে তাঁরা কোনদিনও স-শরীরে দেখতে না পেলেও, তাঁর রচনাবলীর এবং তৎকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারায়, গৈরিক বসনের দ্যুতিতে অগ্নিময় বিবেকানন্দকে তাঁরা তাঁদের মনের মণিকোঠায় অবশ্যই দেখতে পেয়েছিলেন। তা না হলে তখন অমন দুঃসাহসিক কর্মে তাঁদের পক্ষে অনায়াসে ঝাঁপ দেওয়া যেমন সম্ভবপর হত না; তেমনি জীবনের জয়গান গেয়ে হাসতে হাসতে বীরোচিত গর্বে ফাঁসির রজ্জু নিজের কণ্ঠে ধাবণ করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সেই কারণেই উক্ত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন চিত্তে লিখতে পেরেছিলেন, “আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি – দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদেব চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়। তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে সেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।” (১৯২৮ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে ডাঃ. সরসীলাল সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি) রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের মধ্যে দিয়ে মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী যুবকদের প্রতি বিবেকানন্দের অমেয় প্রভাব যে কতটা স্বতোচ্ছল ছিল, সেটা বুঝতে পারা যায়। বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র ঘোষের স্বীকারোক্তিতে বিবেকানন্দ-বহ্নিশিখার যে উত্তাপ অনুভব করা গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের অভিমত – সেসবেরই যথার্থ স্বীকৃতি ছিল। ১৯০১ সালের মার্চ মাসে তরুণ হেমচন্দ্র (পরবর্তীকালে বিপ্লবী মহানায়ক) বিবেকানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে যে নির্দেশ শুনেছিলেন সেটা ছিল – “সর্বপ্রথম চরিত্রবান হও। ভারতমাতার সেবা যদি করিতে চাও তাহা হইলে বীর্যবান হও, দেশমাতৃকার দুর্গতি দূর করিবার জন্য প্রচণ্ড শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হও। সাহস অবলম্বন করিয়া স্ব-স্ব কর্ম করিয়া যাও। জয় তোমাদের অনিবার্য।” (রাখাল বেনু পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ) নিজের মৃত্যুর একটি বছর আগে দেওয়া বিবেকানন্দের সেই নির্দেশ শুধু নির্দেশ ছিল না, সেটা ছিল তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে রক্ষিত অগ্নিবীণার ঝংকার। সেই ঝংকার কেউ কান পাতলেই শুনতে পেতেন না, যাঁর অন্তরে বারুদ ভর্তি থাকত, তিনিই সেটা শুনতে পেতেন। যেমন ‘নিবেদিতা’ সেই ঝংকার শুনতে পেয়েছিলেন – “যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভাবতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে … এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা নয়। দেশ ও জাতির দুর্দশা-নিবারণের প্রামাণ্য প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনা ভোগ।” (বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, মোহিতলাল মজুমদার, পৃ- ১০) বিবেকানন্দের সেই যন্ত্রণা ও অগ্নিদাহের উত্তাপকে নিজেদের ব্যক্তিজীবনে প্রবাহিত করে দিয়ে পরাধীন ভারতের বিপ্লবী তরুণ দল মাতনযজ্ঞে মেতে উঠেছিলেন। আত্মাহুতি সেই যজ্ঞে স্বাভাবিকতার প্রসারণ ঘটেছিল। সেই তরুণ বিপ্লবীরা বিবেকানন্দের পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে বিবেকানন্দের রক্তিম মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে, অন্যদিকে সংঘজননীর অপরিমেয় আশীর্বাদকে পাথেয় করে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

তৎকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের নেত্রী শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে বিবেকানন্দের মতই স্বাধীনতা আত্মার সংগীত ছিল। নিবেদিতার বক্তব্যনুসারে তিনি ছিলেন, ভারতীয় নারীর পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নতুন আদর্শের অগ্রদূত, সেই শ্রীমার দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহা তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। জয়রামবাটীর মাটি তাঁর কাছে চিরপবিত্র ছিল। সেই জয়রামবাটীর পবিত্রভূমিকে প্রণাম করে তাই তিনি বলেছিলেন, “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।” (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ- ৩৬৮) শ্রীমার গোটা জীবনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে তাঁর স্বাধীনচেতা মানসিকতাটি দেখতে পাওয়া যায়। জগজ্জননী হয়েও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত সহমর্মিতার রূপরেখাটিকে তাই এভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর জীবিতাবস্থায় সেই সময়ের বিপ্লবী তরুণ দল কি উদ্বোধনে, কি জয়রামবাটীতে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে গেলে তাঁদের জন্য কোনো দিনই তাঁর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় নি। পুলিশ বিপ্লবীদের সাথে তাঁর সাক্ষ্যাতের গোপনে খবর পেয়ে তাঁকে ‘স্বদেশীদের’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানিয়েছিলেন – “কে স্বদেশী, কে বিদেশী জানিনে। যাঁরা আমার কাছে আসে তাঁরা সকলেই আমার সন্তান।” (শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, স্বামী সারদেশানন্দ, পৃ- ১৬৬) শ্রীমা কখনোই ইংরেজ-শাসনকে সুনজরে দেখেন নি। তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনই তৎকালীন ভারতের দুঃখ-দুর্দশার, অভাব-অনটনের মূল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯১৪-১৮) সাবা দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়েছিল। তখন খাদ্যাভাব, বিশেষতঃ বস্ত্রাভাবে মানুষ-মানুষীর দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। শ্রীমা তখন বস্ত্রাভাবে নারীদের অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের কথা জেনে নিজে চরকায় সুতো কাটবার অভীপ্সার কথা জানিয়েছিলেন। মিশনের কোয়ালপাড়া আশ্রমে তাঁত ও চরকার মাধ্যমে বস্ত্র বয়নের কাজে শ্রীমা আশ্রমকর্মীদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। বিলাতী দ্রব্য-বস্ত্র বর্জন ও তাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা তীব্র হওয়ায় মা সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দিয়ে তাঁত ও চরকার মাধ্যমে বস্ত্র বয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন। (শ্রীশ্রী সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ২৮৪-৮৫) তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া পড়েছিল। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁরই নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় বস্ত্র বিতরণের কাজে নেমেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সম্পর্কে শ্রীমার টুকরো টুকরো কথাগুলি আজও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য – (ক) “ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো!” (শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, স্বামী সারদেশানন্দ, পৃ- ১৬৬) (খ) “আগে ওদের ধ্বংস হবে – নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।” (ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের সাক্ষাৎকার, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ সাল) পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রামকে শ্রীমা ‘ঠাকুরেরই কাজ’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ‘বিপ্লবী সুরেন করের’ আত্মহত্যার কথা শুনে তিনি বলে উঠেছিলেন – “ঠাকুর আর কতদিন অনাচার সইবো।” (Prabuddha Bharata, Vol – IX, 1954, P: 458-80) তখন মুক্তি সংগ্রামে ক্লান্ত-হতাশাময় জীবনে শান্তিলাভের আশায় বিপ্লবী যুবকেরা মাঝে মাঝেই শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে শান্তিলাভের আশায় ছুটে যেতেন। জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী ‘ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়’ তাঁর ‘স্বরাজ’ পত্রিকায় এই প্রসঙ্গটি অন্য ভাবে, ভিন্ন ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। (সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পৃ- ১৭) অনুশীলন সমিতির তরুণ বিপ্লবীরা শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশীর্বাদ নিয়েই শুধু ফিরতেন না, তাঁরা তখন রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়মিত আসা-যাওয়াও করতেন। বিশেষতঃ ঠাকুর-স্বামীজীর আবির্ভাব তিথি উৎসবে তাঁরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতেন। শেষপর্যন্ত তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শ্রীমার অনুমোদনে এবং শ্রীমার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন ও পরবর্তীকালে মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন – দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), নগেন্দ্ৰনাথ সরকার (স্বামী সহজানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) রাধিকা গোস্বামী (স্বামী সুন্দরানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (স্বামী সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ – ভরত মহারাজ) প্রমুখ। পরবর্তী কালে নিতাই দাস (স্বামী বলদেবানন্দ) প্রমুখ আরো অনেক বিপ্লবী যুবক রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁদের বিপ্লবী জীবন থেকে সন্ন্যাসী জীবনে উত্তরণ দেশ তথা সর্ব মানবের সেবায় আত্মনিয়োগের পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিল। তাঁদের মধ্যে দুই বিপ্লবী – দেবব্রত বসু ও শচীন্দ্রনাথ সেন ১৯০৯ সালের মানিকতলা বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত সেই দুই বিপ্লবীকে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের অনুমতি দেওয়াটা যে কতটা বিপজ্জনক ছিল তা সহজেই এখন অনুমেয়। শ্রীমা সারদাদেবী সেদিন সেটা বিপজ্জনক জেনেও ওই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। লোকজননী-দেশজননী-সংঘজননীর পক্ষে সেকাজ সম্ভব হলেও, ওই সূত্রেই রামকৃষ্ণ মিশন রাজরোষবৃদ্ধির কবলে পড়েছিল। পরে সংঘজননীর তৎপরতাতেই তা থেকে মিশন আপাত মুক্ত হয়েছিল। তখনকার অন্যান্য দলের বিপ্লবীরা, এবং অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগ্রামীরাও শ্রীমার চরণস্পর্শে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। জেলে যাওয়ার আগে ও পরে তাঁরা দলে দলে শ্রীমার চরণ স্পর্শ করতে আসতেন। স্বয়ং নিবেদিতা তাঁর চিঠিতে সে কথা জানিয়েছিলেন। (Letter of Sister Nivedita, Edited by Sankari Prasad Basu, Vol – II, P: 990-1000) তাঁরা বিবেকানন্দ জননী – রামকৃষ্ণ সংঘের সংঘজননীর চরণ স্পর্শের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের প্রেরণাকে আরো বেশি করে নিজেদের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সঞ্চারিত করে দিতে চাইতেন। ‘বাঘাযতীন’ (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) উড়িষ্যার বুড়ি বালামের তীরে নিজের দু’জন সতীর্থের সাথে বিশাল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে মাউজার পিস্তল নিয়ে অসম লড়াই করতে যাওয়ার আগে শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রণাম করে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীমার কাছে বাঘাযতীন ছিলেন – ‘আগুনে ছেলে’। বাংলার ইতিহাসে ‘ননীবালাদেবী’র কথা আজও সর্বজনবিদিত। অনুশীলন সমিতির ‘দীনেশ দাশগুপ্ত’ (স্বামী নিখিলানন্দ) এবং যুগান্তর দলের ‘ব্রহ্মচারী গৌরহরি’ মায়ের দীক্ষা ও মিশনে যোগ দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের ‘সুরেশ চৌধুরী’কে ব্রিটিশ পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরদারীর মধ্যেই শ্রীমা দীক্ষা দিয়েছিলেন, এবং অকুতোভয় চিত্তে তাঁকে কোয়ালপাড়া আশ্রমে রাত্রিবাসও করতে দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে শত শত যুবক যখন কারারুদ্ধ ও অন্তরীণ হয়েছিলেন, দেশ যখন যুদ্ধকালীন নানা স্বৈরাচারী আইনের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময়ে বাংলার গভর্ণর জেনারেল ‘লর্ড কারমাইকেল’ তাঁর ‘বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টের’ ভিত্তিতে ওই বছরের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের দরবারী ভাষণে, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বিষোদ্গার করেছিলেন। সেই বিষোদগারের ফলে রামকৃষ্ণ মিশনের অস্তিত্ব তখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তখন অনেকেই সেদিন প্রাক্তন বিপ্লবীদের, যাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁদের তৎক্ষণাৎ মিশন থেকে বিতাড়িত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ‘স্বামী সারদানন্দ’ শ্রীমাকে সেসব কথা জানানোর পরে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, “ওমা! এসব কি কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের-দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছে, তাঁরা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।” (উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃ- ২০৩) এরপরে স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের কথামতো লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিস্তৃত ভাবে লিখে সবকিছু জানানোর পরে গভর্ণর জেনারেল শেষপর্যন্ত ১৯১৭ সালের ২৬শে মার্চ তারিখের একটি চিঠি লিখে তাঁর আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সেবারে সংঘজননীর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ত্বের ফলে রামকৃষ্ণ মিশন রাজরোষে আশু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। তবে তারপরেও ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহের তীরটি কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে তাক করাই ছিল। অন্ততঃ ‘টিনড্যাল, ‘স্টিফেনসন ও লায়নের নোট’; ‘কার, সিডিসন ও রাউলাট রিপোর্ট’ সেটারই ইঙ্গিত বহন করে। ঐতিহাসিক ‘রমেশচন্দ্র মজুমদার’ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনাকালে নানা সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে জানিয়েছিলেন যে, একটা সময়ে ব্রিটিশ সরকার ‘ভারতরক্ষা আইন’-এ রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত নানা কারণে সেটা সম্ভব হয়নি।
(পরের পর্বে সমাপ্ত)
(তথ্যসূত্র: লেখার মাঝে উল্লেখিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সমূহ)